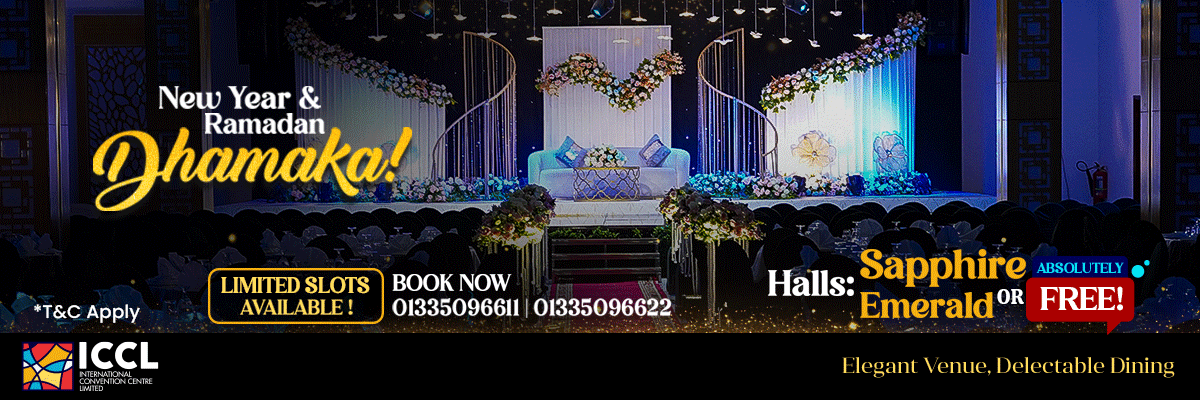বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী-তরুণ প্রজন্মের অনুপ্রেরণা

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী তরুণ প্রজন্মের জন্য একটি অনুপ্রেরণার উৎস, যা দেশপ্রেম, সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং জাতীয় সংকট মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বহু ত্যাগ, রক্তঝরা সংগ্রাম ও সীমাহীন তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-রচিত হয়েছে বাঙালি জাতির ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যায়। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। লাখ লাখ শহীদের আত্মদান, অসংখ্য মা–বোনের অবর্ণনীয় ত্যাগ এবং কোটি মানুষের দুর্ভোগের বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে বিজয় অর্জিত হয়।
বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর বীরত্ব, সাহসিকতা ও নেতৃত্ব এই বিজয়ের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ। একটি প্রশিক্ষিত ও সুসজ্জিত বাহিনীর বিরুদ্ধে মাত্র নয় মাসে যুদ্ধজয় পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল ঘটনা। এ বিজয়ের পেছনে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। সেনাবাহিনী ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যেন একই মুদ্রার এপিঠ–ওপিঠ; তাদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগ জাতির আস্থা, গর্ব ও ভালোবাসার প্রতীকে পরিণত করেছে সশস্ত্র বাহিনীকে।
আরও পড়ুন: নির্বাচনের ছায়ায় রক্তাক্ত রাজনীতি: সহিংসতার অদম্য প্রবণতা
১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার মানুষ নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতার মুখোমুখি হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বহু তরুণ আকাঙ্ক্ষা, দেশপ্রেম ও দায়িত্ববোধ থেকে পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু শুরুর দিক থেকেই পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীতে বাঙালি সদস্যদের প্রতি আচরণ ছিল বৈষম্যমূলক ও অবমাননাকর। সামরিক বাহিনীর উচ্চপদগুলো পশ্চিম পাকিস্তানের কর্মকর্তারা দখলে রাখতেন; বাঙালি কর্মকর্তারা সমান বা অধিক যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও পদোন্নতি ও দায়িত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে বঞ্চিত হতেন।
পাকিস্তানি সামরিক মহলে প্রচলিত ভুল ধারণা ছিল—বাঙালিরা শারীরিকভাবে দুর্বল, যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত নয় এবং তাদের প্রতি ভরসা করা যায় না। ফলে প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক দায়িত্ব—সব জায়গায়ই বাঙালিদের পিছনে ঠেলে দেওয়া হতো। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙালি ইউনিটগুলোর কাছে পাঠানো হতো পুরোনো ও নিম্নমানের অস্ত্র, যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের ইউনিটগুলো পেত আধুনিক ও উন্নত অস্ত্রশস্ত্র।
আরও পড়ুন: ফেব্রুয়ারি: ভাষার স্মৃতি, বর্তমান ও আমাদের দায়
এই বৈষম্য ছিল শুধুই সামরিক কাঠামোর অভ্যন্তরীণ সমস্যা নয়; এটি ছিল সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় শাসনেরই প্রতিচ্ছবি। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বৈষম্য পূর্ব পাকিস্তানকে ক্রমাগত দমিয়ে রেখেছিল, একই শোষণের ছাপ দেখা যেত সশস্ত্র বাহিনীতেও। এর ফলে বাঙালি সেনাদের হৃদয়ে ক্ষোভ, বেদনা ও অসন্তোষ ক্রমে জমতে থাকে।
১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ গভীর রাতের অন্ধকার চিরে দখলদার বাহিনী নিরস্ত্র, নিরীহ ও ঘুমন্ত বাঙালির ওপর শুরু করে ইতিহাসের অন্যতম গণহত্যা। বাঙালি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত এই সুপরিকল্পিত ও ন্যায়নীতি বহির্ভূত নৃশংস হত্যাযজ্ঞই ‘অপারেশন সার্চলাইট’ নামে কুখ্যাত; যা এই ক্ষোভকে বিষ্ফোরিত করে। ঢাকাসহ সারা দেশে নির্বিচারে গণহত্যা, নারী নির্যাতন এবং ধ্বংসযজ্ঞ বাঙালিদের অস্তিত্ববিরোধী রূপ ধারণ করে। এই বর্বর হামলার পরপরই ২৬ মার্চ ভোরে মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নেই হানাদার বাহিনীর আক্রমণের জবাবে বাঙালি অফিসার ও সৈনিকরা ভীত বা স্তম্ভিত না হয়ে সাহসিকতার সঙ্গে বিদ্রোহে অবতীর্ণ হন এবং সরাসরি মুক্তিসংগ্রামে অংশ নেন; যা বিশ্ব সামরিক ইতিহাসে অন্যতম বিরল ঘটনা।
২৫ মার্চ রাতে চট্টগ্রামের ষোলশহরে অবস্থানরত ৮ম ইস্ট বেঙ্গল, ২৬ মার্চ দিনে কুমিল্লার ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল, ২৭ মার্চ জয়দেবপুরের ২য় ইস্ট বেঙ্গল, ২৮ মার্চ যশোরের ১ম ইস্ট বেঙ্গল এবং সৈয়দপুরের ৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করে মুক্তিযুদ্ধের পতাকাতলে যুক্ত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত এই পাঁচটি পদাতিক ব্যাটালিয়নই পরবর্তীতে মুক্তিবাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামোর মেরুদণ্ডে পরিণত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে কর্মরত বহু কর্মকর্তা জীবনবাজি রেখে পালিয়ে আসেন; ছুটিতে থাকা অনেক বাঙালি সেনা সরাসরি যুদ্ধে আত্মনিয়োগ করেন। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর সদস্য এবং অসংখ্য সাধারণ মানুষ; যাদের অধিকাংশেরই সামরিক প্রশিক্ষণ ছিল না। মাতৃভূমির মুক্তির স্বার্থে তারা জীবন বাজি রেখে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেন। এর মধ্য থেকেই জন্ম নেয় একটি সংগঠিত সশস্ত্র মুক্তিবাহিনীর ধারণা।
পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাধুনিক অস্ত্র ও প্রশিক্ষণের তুলনায় বাঙালির সামরিক শক্তি ছিল কম, কিন্তু তাদের মনোবল, দেশপ্রেম এবং জনসমর্থন ছিল অপরিসীম। এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেই বাঙালি সেনারা প্রচলিত যুদ্ধনীতির বাইরে গিয়ে গড়ে তোলে গেরিলা যুদ্ধ; যা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শক্তিশালী কাঠামোকে ধীরে ধীরে দুর্বল করতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকে মাত্র কয়েক হাজার প্রশিক্ষিত সেনাকে নেতৃত্ব দিতে হয়েছিল লক্ষাধিক মুক্তিকামী সাধারণ মানুষকে। এই সময়ই সেনাবাহিনীর সদস্যরা হয়ে ওঠেন যুদ্ধের কৌশলী, সংগঠক, প্রশিক্ষক এবং মাঠ-যোদ্ধা; সবকিছু একসঙ্গে। ফলে গেরিলা যুদ্ধ সংগঠিত ও পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।
প্রাথমিক প্রতিরোধকে সুশৃঙ্খল সামরিক কাঠামোয় রূপ দেওয়ার প্রথম দৃশ্যমান পদক্ষেপ ছিল ১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিলের তেলিয়াপাড়া সম্মেলন। সিলেটের হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর থানার তেলিয়াপাড়া চা বাগানের ম্যানেজার বাংলোয় অনুষ্ঠিত এ ঐতিহাসিক সভায় কর্নেল এম এ জি ওসমানীকে মুক্তিযোদ্ধাদের কমান্ডার ইন চিফ হিসেবে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। সেই সঙ্গে গৃহীত হয় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠন, অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ, সীমান্তবর্তী এলাকাগুলো ব্যবহারের অনুমতি, একক কমান্ড চ্যানেল প্রতিষ্ঠা, মুক্তিযুদ্ধ মনিটরিং সেল গঠন, সামরিক অঞ্চল বিভাজন এবং কমান্ডার নিয়োগসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। পরবর্তীতে ১০ এপ্রিল তেলিয়াপাড়ায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সামরিক বৈঠকে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশকে ছয়টি সামরিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়।
১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ পায় পরিকল্পিত দিকনির্দেশনা। এরপর ১০–১৭ জুলাই অনুষ্ঠিত সেক্টর কমান্ডারদের সম্মেলনে যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার্থে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টর ও বহু সাব-সেক্টরে বিভক্ত করে প্রতিটি অঞ্চলের দায়িত্ব দক্ষ, দুরন্ত ও অসীম সাহসী সেক্টর কমান্ডারদের ওপর ন্যস্ত করা হয়।
যুদ্ধের এক পর্যায়ে মে মাসের শেষ নাগাদ কর্নেল এম এ জি ওসমানী গেরিলা যুদ্ধের বিষয়ে চিন্তা করেন এবং জুন ১৯৭১ মাসের মধ্যে তিনি গেরিলা ফোর্স গঠন করে মুক্তিযুদ্ধকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে যান। গেরিলাদের হাতে সাধারণত স্বল্পপাল্লার অস্ত্র ছিল, কিন্তু তাদের মনোবল ছিল অটল। দেশপ্রেমের প্রেরণায় তারা শত্রুর অবস্থানে আঘাত হেনে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সরবরাহ ব্যবস্থাকে বারবার ক্ষতিগ্রস্ত করে। এর ফলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী দেশের ভেতরে কার্যত অচল হয়ে পড়তে থাকে। এই কৌশল শত্রুর মনোবল ভাঙতে, কার্যক্রম পরিচালনা ব্যাহত করতে এবং যুদ্ধের গতি নিজের পক্ষে আনতে অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়। সেক্টরগুলোর পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের শেষভাগে সুসংগঠিত নিয়মিত যুদ্ধ পরিচালনার জন্য পরবর্তীতে ‘জেড ফোর্স’, ‘এস ফোর্স’ ও ‘কে ফোর্স’ নামে তিনটি নিয়মিত ব্রিগেড গঠন করা হয়। এই তিন ফোর্স মুক্তিযুদ্ধের সিদ্ধান্তমূলক মুহূর্তগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।
জেড ফোর্স: লে. কর্নেল জিয়াউর রহমানের (পরবর্তী সময়ে সেনাপ্রধান) নেতৃত্বে গঠিত জেড ফোর্স ছিল মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সংগঠিত বাহিনীগুলোর একটি। ১ম, ৩য় ও ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে গঠিত এই বাহিনী সিলেট, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও জামালপুর অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। বিশেষ করে টাঙ্গাইলের যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের জয় পাকিস্তানি বাহিনীর মনোবল ভেঙে দেয় এবং মুক্তিবাহিনীর অগ্রযাত্রা ত্বরান্বিত করে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করার ক্ষেত্রে জেড ফোর্স ছিল পথিকৃৎ। জেড ফোর্সের অধীনে এই অঞ্চলে পরিচালিত সব সফল অপারেশন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করেছে।
এস ফোর্স: লে. কর্নেল কে এম শফিউল্লাহর নেতৃত্বে গঠিত এস ফোর্স (২য় ও ১১তম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট) ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সরাইল, আখাউড়া ও হবিগঞ্জ এলাকায় কার্যক্রম পরিচালনা করে। তাদের কৌশল ছিল শত্রুর সরবরাহ ব্যবস্থা ধ্বংস করা, আক্রমণ করে অবস্থান দুর্বল করা এবং ঢাকার দিকে অগ্রযাত্রার পথ সুগম করা। এস ফোর্সের সাফল্যের ফলে পূর্বাঞ্চলের যুদ্ধে নাটকীয় গতি সৃষ্টি হয়।
কে ফোর্স: লে. কর্নেল খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে গঠিত কে ফোর্স (৪র্থ, ৯ম ও ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট) ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও ফরিদপুর অঞ্চলে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান পরিচালনা করে। নিয়মিত বাহিনী ও গেরিলাদের সমন্বয়ে পরিচালিত তাদের কৌশল পাকিস্তানি বাহিনীর শক্ত ঘাঁটিগুলোকে দুর্বল করে তোলে। ফলে মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাঞ্চলীয় ফ্রন্টে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সম্ভব হয়।
মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে নৌবাহিনীর সদস্যরা বিভিন্ন সেক্টরে নিয়মিত বাহিনীর সঙ্গে সম্মিলিতভাবে অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ফ্রান্স থেকে পালিয়ে আসা কয়েকজন বাঙালি নাবিকও স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেন। এছাড়া পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে ছুটিতে এসে আটকা পড়া নৌসদস্যরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে স্বাধীন নৌবাহিনী গড়ে তোলার স্বপ্নে আত্মনিয়োগ করেন। আগস্ট মাসে বিভিন্ন সেক্টরে ছড়িয়ে থাকা নৌসদস্যদের কলকাতায় সমবেত করা হয় এবং প্রশিক্ষণের জন্য হুগলি নৌঘাঁটিতে পাঠানো হয়। যুদ্ধের শুরু থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত মোট ৫১৫ জন নৌ-কমান্ডোকে বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অপারেশন পরিচালনার উপযোগী করে তোলা হয়।
আগস্টের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত এসব সাহসী কমান্ডো বহু দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনা করেন। পাকিস্তানি যুদ্ধজাহাজসহ একাধিক নৌযানে ক্ষয়ক্ষতি সাধন করেন তারা। এর মধ্যে ১৫ আগস্ট ১৯৭১-এর ‘অপারেশন জ্যাকপট’ ছিল নৌবাহিনীর ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত—একই দিনে দেশের পাঁচটি বন্দরে মোট ২৬টি জাহাজ সফলভাবে ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হয় মুক্তিযোদ্ধারা। কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত দুটি টাগবোটকে ‘গার্ডেন রীচ ডকইয়ার্ড’-এ যুদ্ধজাহাজে রূপান্তরিত করা হয় এবং যথাক্রমে ‘পদ্মা’ ও ‘পলাশ’ নামে নামকরণ করা হয়।
১৯৭১ সালের মে মাসের শেষ দিকে উইং কমান্ডার এ কে খন্দকার একদল অফিসার ও টেকনিশিয়ানসহ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। উইং কমান্ডার খন্দকারকে মুক্তিবাহিনীর ‘ডেপুটি চিফ অব স্টাফ’ পদে নিয়োগ দিয়ে প্রশিক্ষণ ও অপারেশন পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। মাত্র তিন-চারটি হালকা বিমান ও হেলিকপ্টার এবং দশ-বারোজন পাইলট ও টেকনিশিয়ানকে নিয়ে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিমান শক্তি। পরবর্তীতে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা ১৭ জন অফিসার এবং ৫০ জন বিমানসেনা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্রদানকৃত একটি অটার, একটি ডিসি-৩ বিমান এবং একটি অ্যালুয়েট হেলিকপ্টারসহ ২৮ সেপ্টেম্বর ভারতের ডিমাপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় বাংলাদেশ বিমান বাহিনী। ‘বাংলার আকাশ রাখিব মুক্ত’; এই অঙ্গীকার বুকে ধারণ করে শুরু হয় বীর বাঙালির আকাশযুদ্ধের অগ্রযাত্রা।
প্রথাগত যুদ্ধ শুরু করার জন্য ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর সেনাবাহিনীর সঙ্গে নৌ ও বিমানবাহিনী সম্মিলিতভাবে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে এক দূরদর্শী সম্মিলিত আক্রমণের মাধ্যমে চলমান যুদ্ধে নতুন গতিশীলতা আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯৭১ সালের নভেম্বরের দিকে মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বিত আক্রমণে পাকিস্তানি বাহিনীর মনোবল ভেঙে যায় এবং তারা পিছু হটতে শুরু করে। একই সময়ে মুক্তিবাহিনী সমন্বিত আক্রমণ জোরদার করে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হয়।
১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ যৌথবাহিনী ঢাকা অভিমুখে অগ্রযাত্রা শুরু করলে পাকিস্তানি বাহিনী দ্রুত কোণঠাসা হয়ে পড়ে। অবশেষে ১৬ ডিসেম্বর বিকেল ৫টা ১ মিনিটে রমনা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) প্রায় ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে। যৌথবাহিনীর পক্ষে স্বাক্ষর করেন লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এবং পাকিস্তানি বাহিনীর পক্ষে লে. জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজী। বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার। এই আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়েই বিশ্বের মানচিত্রে জন্ম নেয় স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র—আমাদের প্রাণপ্রিয় বাংলাদেশ।
১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ শুধু একটি রাষ্ট্রীয় পরাজয় ছিল না; এটি ছিল বাঙালির দীর্ঘ শোষণ, বৈষম্য ও অবমাননার বিরুদ্ধে এক ঐতিহাসিক জয়ের ঘোষণাপত্র। এর মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় স্বাধীন বাংলাদেশ; যার অস্তিত্ব রক্ষায় এবং জন্মলগ্নে নেতৃত্ব প্রদানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ছিল অগ্রভাগে।
স্বাধীনতার পর রাষ্ট্র পুনর্গঠন, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ; সব সংকটময় সময়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে। দেশের অখণ্ডতা রক্ষা, পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও সন্ত্রাস দমনে সেনাসদস্যরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। র্যাব ও বিজিবির সঙ্গে সমন্বিতভাবে জঙ্গিবাদ দমন এবং সীমান্ত সুরক্ষায় তাদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও আধুনিকায়নেও সেনাবাহিনীর ভূমিকা অনন্য। ছবিসহ ভোটার তালিকা, জাতীয় পরিচয়পত্র এবং মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট তৈরিতে তাদের দক্ষতা আন্তর্জাতিক প্রশংসা পেয়েছে। পদ্মা সেতু, জাতীয় মহাসড়ক, মেট্রোরেল, রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্প, পূর্বাচল এক্সপ্রেসওয়ে, হাতিরঝিল, মেরিন ড্রাইভসহ গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় অবকাঠামো নির্মাণে তারা নির্ভরযোগ্য অংশীদার হিসেবে কাজ করেছে।
মানবিক সহায়তায় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী সবসময়ই জনগণের প্রথম ভরসা। সিডর, আইলা, আম্পান বা ২০২৪ সালের ফেনী–কুমিল্লার ভয়াবহ বন্যা—সব দুর্যোগেই তারা উদ্ধার, ত্রাণ ও পুনর্বাসনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। করোনা মহামারির সময়ও মাঠপর্যায়ে লকডাউন, চিকিৎসা ও কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থায় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর নিষ্ঠা জাতীয়ভাবে প্রশংসিত হয়।
আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা আজ বিশ্বে সম্মানিত একটি নাম। সুদান, মালি, কঙ্গো, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, কম্বোডিয়া, কসোভো, জর্জিয়া, পূর্ব তিমুর, সিয়েরালিওন, লাইবেরিয়া, আইভরিকোস্ট, হাইতি, লেবাননসহ বিভিন্ন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে তারা শান্তি প্রতিষ্ঠা, পুনর্বাসন ও মানবিক সহায়তায় অসাধারণ সাফল্য দেখিয়েছে। এসব অবদানে আজ বাংলাদেশকে শান্তিরক্ষার ‘মডেল দেশ’ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী অস্থির পরিস্থিতি মোকাবিলায় সেনাবাহিনী অত্যন্ত দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে। বর্তমান সেনাপ্রধান স্থিতিশীল নেতৃত্বের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। সময়ের সঙ্গে নিজেদের আধুনিকীকরণে সেনাবাহিনী আজ একটি সুসংগঠিত ও উচ্চমানের বাহিনী। নতুন পদাতিক ডিভিশন, আধুনিক সমরাস্ত্র, প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থা এবং শিক্ষা-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান; সব মিলিয়ে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী আজ দেশের গর্ব ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সম্মানিত শক্তি।
মহান মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাঙালির আত্মপরিচয় ও স্বাধীন অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। এ যুদ্ধে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী অসামান্য সাহস, সংগঠনক্ষমতা ও দূরদর্শী নেতৃত্বের পরিচয় দেয়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নিপীড়ন ও গণহত্যার বিরুদ্ধে বাঙালি সেনাদের অদম্য বীরত্ব বিশ্ব ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত। স্বাধীনতা যুদ্ধে তাদের সেই মহত্তম অবদান এবং পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে তাদের সফল অংশগ্রহণ তরুণ সমাজে দেশপ্রেম, মানবিকতা ও দায়িত্ববোধকে আরও দৃঢ় করেছে।
সময়ের সঙ্গে প্রযুক্তি নির্ভরতা ও পেশাগত উৎকর্ষে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী পরিণত হয়েছে বিশ্বমানের এক আধুনিক বাহিনীতে। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভূখণ্ডের অখণ্ডতা রক্ষায় তাদের অটল অঙ্গীকার- শৃঙ্খলা, দেশপ্রেম ও কর্মনিষ্ঠার উজ্জ্বল উদাহরণ। ফলে সশস্ত্র বাহিনী আজ কেবল একটি বাহিনী নয়; এটি জাতির আস্থা, গৌরব ও বিজয়ের চিরন্তন প্রতীক।