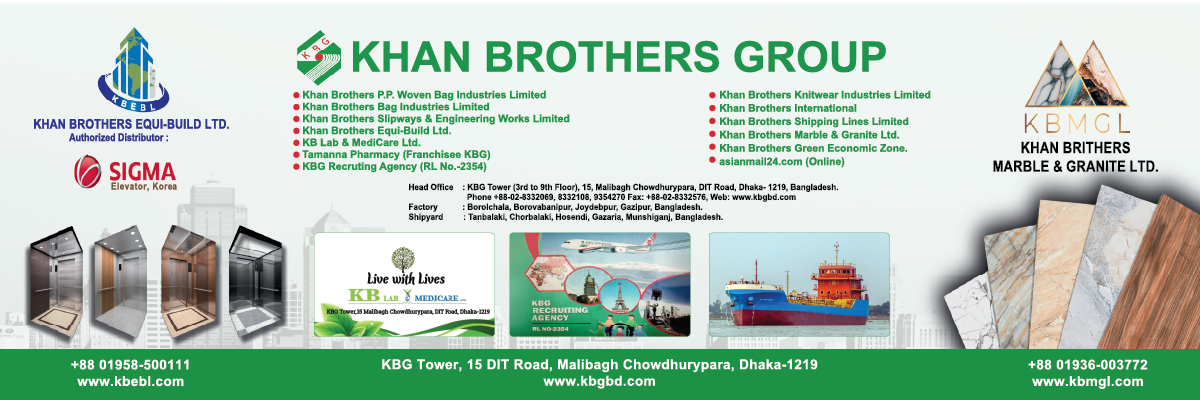সংস্কার প্রসঙ্গ: রাজনৈতিক দলের একক সিদ্ধান্ত জনগণের ইচ্ছা হতে পারে না

বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক সংস্কার ও শাসনব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস নিয়ে আলোচনা চলছে।কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়—এই প্রক্রিয়াগুলোর কতটুকু বাস্তবতা ভিত্তিক? কতটুকু অংশগ্রহণমূলক?
বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কার এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নানা নামে গঠিত হচ্ছে “সংস্কার কমিশন”, চলছে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কথিত “সংলাপ” ও “ঐকমত্য” প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। কিন্তু এই প্রক্রিয়াগুলোর কতটা বাস্তবভিত্তিক, কতটা অংশগ্রহণমূলক এবং সর্বোপরি—এসবের মাধ্যমে সত্যিকার জনগণের মতামত কি আদৌ প্রতিফলিত হচ্ছে?
আরও পড়ুন: গণ আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে হতাশার মুখোমুখি
বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কার যদি গণতন্ত্রের ভিত্তি মজবুত করার লক্ষ্যে হয়, তবে সেটি হতে হবে জনগণের মতের ভিত্তিতে—দলীয় মত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থে নয়। কারণ, প্রজাতন্ত্রের মালিক রাজনৈতিক দল নয়—জনগণ।
রাজনৈতিক বাস্তবতাঃ- গোষ্ঠীস্বার্থের গণতন্ত্র বনাম জনস্বার্থের গণতন্ত্র
আরও পড়ুন: জম্মু-কাশ্মীর: আলাদা পরিচয় থেকে জাতীয় মূলধারায়
বাংলাদেশে বর্তমানে ৪৪টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল রয়েছে (তথ্যসূত্র: নির্বাচন কমিশন, ২০২৪)। বাস্তবে মাঠপর্যায়ে সক্রিয় দল ৫-৬টি মাত্র। অধিকাংশ দলের নেই সংগঠন, নেই কোনো সক্রিয় কর্মী, এমনকি কয়েকটির সদস্য মাত্র দুই-তিনজন। অথচ জাতীয় ঐক্যমতের নামে এসব দলও দপ্তরঘরের টেবিলে বসে জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে।
এই প্রশ্ন এখন সময়ের দাবি: একজন করদাতা নাগরিক, একজন ভোটার, যিনি প্রতিদিন দেশ চালাতে রাজস্ব দিচ্ছেন—তিনি কোথায়? তাঁর মতামত কে নিচ্ছে? তাঁর পক্ষে কে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে?
প্রতিনিধিত্ব কি এমন ব্যক্তির মাধ্যমে হবে—যিনি
• রাজনীতিকে পেশা বানিয়েছেন,
• আয়ের কোনো বৈধ উৎস নেই,
• ট্যাক্স দেন না,
• বিলাসবহুল জীবনযাপন করেন,
• রাজনীতির আড়ালে চাঁদাবাজি, কমিশন বাণিজ্য ও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেন?
এসব লোক কিভাবে জনগণের প্রতিনিধি হন? আর যখন জনগণ জানে না তারা কাকে প্রতিনিধি বানিয়েছে, তখন সেই প্রতিনিধির সিদ্ধান্ত জনগণের সিদ্ধান্ত হতে পারে না।
“আমার সিদ্ধান্ত আমি নেব”—এই অধিকার কেড়ে নেওয়া যাবে নাঃ-
এই দেশের মালিক জনগণ। আমার সিদ্ধান্ত আমি নেব—এটাই গণতন্ত্রের ভিত্তি। রাজনৈতিক নেতা আমার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার পান তখনই, যখন আমি তাকে সেই অধিকার দিয়েছি। কিন্তু আজকের বাস্তবতায় দেখা যাচ্ছে, দলনির্ভর কমিশন বা সিন্ডিকেটভিত্তিক রাজনৈতিক জোট কিছু সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিচ্ছে জাতির ওপর—যার সঙ্গে জনগণের কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই।
এই অবস্থা চলতে থাকলে সাধারণ মানুষ বারবার বঞ্চিত হবে, এবং একসময় বিদ্রোহ হবে অনিবার্য। আমরা ২০২৪ সালেই দেখেছি কীভাবে ছাত্র সমাজ ও তরুণ প্রজন্ম রাস্তায় নেমেছিল জনগণের অধিকার রক্ষায়। সেই ইতিহাস পুনরাবৃত্তি হোক কেউ চায় না।
জনগণের অবস্থানঃ- রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা ও বঞ্চনার বাস্তব চিত্র
২০২৩ সালে বিআইডিএস পরিচালিত একটি জরিপে দেখা গেছে:
• দেশের ৬২% মানুষ কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য নয়,
• তারা মনে করে রাজনীতির মাধ্যমে তাদের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়,
• তরুণদের মধ্যে এই অনাস্থা আরও প্রকট—৭১% তরুণ কোনো দলের প্রতি আস্থা রাখে না।
এই বাস্তবতায় ‘জাতীয় ঐকমত্য’ বলে যে প্রহসন চালানো হয়, তা স্পষ্টতই গণবিচ্ছিন্ন। বাস্তবে ৮০-৮৫ শতাংশ মানুষের মতামত বাদ দিয়েই ১০-১৫ শতাংশের সিদ্ধান্তকে জনগণের ইচ্ছা বলে চালিয়ে দেওয়া হয়।
গণভোট: গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত আত্মা
ব্রেক্সিট, সুইজারল্যান্ডের আইন সংস্কার, আয়ারল্যান্ডের গর্ভপাত আইন কিংবা ব্রাজিলের বিচার ব্যবস্থা সংস্কার—এইসব সিদ্ধান্ত জনগণ নিয়েছে সরাসরি ভোট দিয়ে। বাংলাদেশ সংবিধানের ৭(১) অনুচ্ছেদ স্পষ্ট করে বলেছে:
“প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ।”
এছাড়াও, সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে বলা আছে:
“প্রজাতন্ত্রে গণতন্ত্রের একটি কার্যকর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে, যেখানে জনগণ সকল কার্যাবলিতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করিবে।”
তাহলে কেন আজ এই জনগণের মতামত ছাড়া, শুধু রাজনৈতিক দলের সিদ্ধান্তে সংস্কার হবে? কেন একটি ‘কমিশন’ দলীয় প্রস্তাবকে ‘জনগণের অভিমত’ হিসেবে স্বীকৃতি দেবে? অথচ, এত বড় সিদ্ধান্ত যেমন সংসদীয় ব্যবস্থার সংস্কার, রাষ্ট্রপতি বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা, জাতীয় নির্বাচন পদ্ধতি—সবই নির্ধারিত হয় রাজনৈতিক দলের মধ্যকার আলোচনায়, অথচ জনগণের ইচ্ছাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না।
গণভোট না হলে কী ঘটতে পারে?
১. জনগণের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার প্রতি আস্থা হারাবে।
২. জনগণ ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিশ্বাসের সংকট গড়ে উঠবে।
৩. বিরোধী মত, ছাত্র সমাজ ও সাধারণ মানুষ নতুন আন্দোলনে নামবে।
৪. ভবিষ্যৎ প্রজন্ম রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে।
৫. আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বাংলাদেশকে স্বচ্ছ গণতন্ত্র চর্চাকারী দেশ হিসেবে দেখতে পাবে না।
৬. রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়বে, যা উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করবে।
৭. সর্বোপরি, এই সংস্কার হবে জনগণের বিরুদ্ধে একটি চাপিয়ে দেওয়া রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র।
সংস্কার কমিশনের প্রতি কঠোর বার্তাঃ-
• আপনি রাজনৈতিক দলের নয়, জনগণের কমিশন।
• আপনি প্রতিনিধি নন, মধ্যস্থতাকারী।
• আপনি জনপ্রতিনিধিত্ব যাচাইয়ের পরীক্ষক, চাটুকার নন।
• আপনি যদি গণভোটের ব্যবস্থা না করেন, তবে ইতিহাস আপনাকে ক্ষমা করবে না।
এই দেশ কারও পারিবারিক প্রতিষ্ঠান নয়। সংবিধান আর সংলাপের ফাঁক গলে দলীয় স্বার্থ রক্ষা নয়—জনগণের রায় নিতে হবে।
উপসংহারঃ- সংস্কার মানে জনগণের রায়, না যে দল বেশি চিৎকার করে তার জয় ?
বাংলাদেশ আর গোষ্ঠীনির্ভর সিদ্ধান্তে ধ্বংস হতে চায় না। জনগণ এখন সচেতন, সংগঠিত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই এখনই সময় “সংস্কার” শব্দটিকে সত্যিকার অর্থে অর্থবহ করে তোলার।
গণভোট ছাড়া কোনো সংস্কার বৈধ নয়, নৈতিক নয়, গণতান্ত্রিক নয়।
অতএব,গণতন্ত্র মানে শুধু নির্বাচন নয়—গণতন্ত্র মানে জনগণের সক্রিয়, প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ।
লেখক : রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও কলাম লেখক।